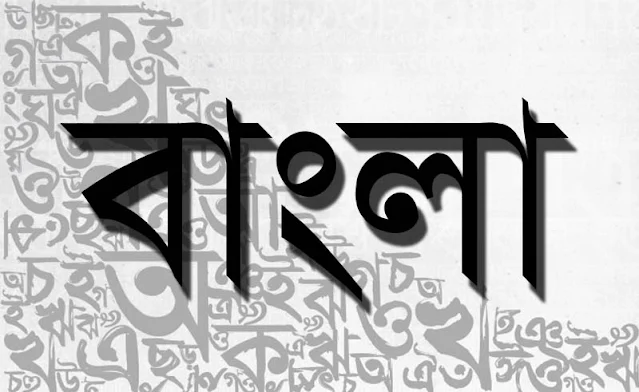Bengali honours1st semester/ 2nd paper/ ভাষা ও সাহিত্যUNIVERSITY OF KALYANI
বাংলা ভাষা বিকাশের ইতিহাস ১৩০০ বছর পুরনো। চর্যাপদ এ ভাষার আদি নিদর্শন। অষ্টম শতক থেকে বাংলায় রচিত সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষে এসে বাংলা ভাষা তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহণ করে। বাংলা ভাষার লিপি হল বাংলা লিপি। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বাংলা ভাষার মধ্যে শব্দগত ও উচ্চারণগত সামান্য পার্থক্য রয়েছে। বাংলার নবজাগরণে ও বাংলার সাংস্কৃতিক বিবিধতাকে এক সূত্রে গ্রন্থনে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে তথা বাংলাদেশ গঠনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
উপভাষা কাকে বলে? কয় প্রকার ও কি কি?? তাদের সীমানা নির্ধারণ কর।
উপভাষা : কোনো একটি ভাষা যদি বৃহত্তর অঞ্চলে বহু সংখ্যক মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, তাহলে অঞ্চলভেদে সেই ভাষার মধ্যেও কিছু কিছু স্বতন্ত্র আঞ্চলিক উচ্চারণবিধি পরিলক্ষিত হয় সেই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই ভাষার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ভাষার রীতিকে বলা হয় উপভাষা। সুকুমার সেন লিখেছেন— কোনো ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোট দল বা অঞ্চলে প্রচলিত বিশেষ ভাষা ছাঁদকে উপভাষা বলে।
শ্রেণীবিভাগ
বাংলা ভাষায় অঞ্চলভেদে ভিন্ন উচ্চারণ হয়ে থাকে, যেমন: পূর্ববঙ্গের একটি উপভাষায় বলা হয়, 'আমি অহন ভাত খামু না' যা আদর্শ বাংলায় বলা হয়, 'আমি এখন ভাত খাব না।' ভাষাবিদ সুকুমার সেন বাংলা উপভাষার শ্রেণীবিন্যাস করেছেন।[১] পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলা ভাষা উচ্চারণ ভিত্তিতে আলাদা। তাই, বাংলা উপভাষা পাঁচ প্রকার:
• রাঢ়ী উপভাষা
• বঙ্গালী উপভাষা
• বরেন্দ্রী উপভাষা
• ঝাড়খণ্ডী উপভাষা
• রাজবংশী উপভাষা
Q:- বঙ্গালী উপভাষার প্রচলনস্থান নির্দেশ কর এবং এই উপভাষার বিশিষ্ট লক্ষণাবলীর পরিচয় দাও।

ঙ)বঙ্গালীর উত্তম পুরুষে ‘ম’ (করুম, যামু)। অতীতকালে রাঢট়ীতে 'লুম', 'লেম' বঙ্গালীতে 'লাম'।
চ)বঙ্গালীতে শব্দভাণ্ডারে মূলতঃ ঐক্য থাকলেও ধ্বনি-তাত্ত্বিক পার্থক্য বর্তমান (রাঢ়ীতে কেষ্ট, ছেরাদ্দ, নেমন্তন, বঙ্গালীতে 'কিশন, ছাদ্দ, নিমন্তন্ন')।
Q:-রাঢ়ী উপভাষার অঞ্চল বা এলাকা উল্লেখ করে এই উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ।
রাঢ়ী উপভাষার অঞ্চল বা এলাকা:
বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের প্রধান উপভাষা
(dialect) রাঢ়ী। যদিও মােটামুটিভাবে রাঢ়ীর দুটি প্রধান বিভাগ-পূর্ব ও পশ্চিম, তবু সূক্ষ্ম বিচারে রাঢ়ীর বিভাগ ৪টি। এগুলি হল:
(ক) পূর্ব-মধ্য (east central) : কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া।
(খ) পশ্চিম-মধ্য (west Central) : পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব বীরভূম, হুগলি, বাঁকুড়া।
(গ) উত্তর-মধ্য (north Central) : মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দক্ষিণ-মালদহ।
(ঘ) দক্ষিণ-মধ্য: উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (ডায়মন্ড হারবার)।
রাঢ়ীর উপভাষার বৈশিষ্ট্য :
(১)রাঢ়ী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (phonological features) :
(ক) ই, উ, ক্ষ এবং য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী অ’-এর উচ্চারণ হয় ‘ও। যেমন—অতি > [ওতি], মধু > [মােধু], লক্ষ > [লােক্খাে], সত্য >[শােত্তো]। অন্য ক্ষেত্রেও অ-কারের ও-কার-প্রবণতা দেখা যায়। যেমন--মন >[মোন], বন > [বােন]।
(খ) পূর্ব বাংলার বঙ্গালী উপভাষায় শব্দের মধ্যে অবস্থিত ‘ই' এবং 'উ' সরেএসে তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে উচ্চারিত হয়। যেমন- করিয়া > কইরা (অর্থাৎ ক্ + অ + র + ই + হ্ + অ > ক্ + অ + ই + র + য + আ)। এই প্রক্রিয়াকে বলে অপিনিহিতি।
এখানে অপিনিহিতির ফলে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে সরে আসা এই ‘ই’ ও ‘উ’ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিশে যায় এবং তার পরবর্তী স্বরধ্বনিকেও পরিবর্তিত করে ফেলে। যেমন—কইর ্যা > করে (ক + অ+ ই +র +য় + আ > ক্ + অ + র + এ) । একে অভিশ্রুতি বলে।
(গ) রাঢ়ীতে স্বরসঙ্গতির ফলে শব্দের মধ্যে পাশাপাশি বা কাছাকাছি অবস্থিত বিষম স্বরধ্বনি সম স্বরধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। দেশি>দিশি (দ + এ+ শ + ই + > দ্ + ই + স্ + ই) ইত্যাদি।
(ঘ) শব্দমধ্যস্থ নাসিক্য ব্যঞ্জন যেখানে লােপ পেয়েছে সেখানে পূর্ববর্তী স্বরের নাসিক্যীভবন ঘটেছে। যেমন বন্ধ > বাঁধ। কোথাও কোথাও নাসিক্য ব্যঞ্জন না থাকলেও স্বরধ্বনির স্বতো নাসিকীভবন দেখা যায়। যেমন—পুস্তক > পুথি >পুঁথি (গ্রন্থ)।
(ঙ) শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের অন্তে অবস্থিত মহাপ্রাণ ধ্বনি( বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ) স্বল্পপ্রাণ (বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ) উচ্চারিত হয়। যেমন—দুধ > দুদ ইত্যাদি।
(চ) শব্দের অন্তে অবস্থিত অঘােষ ধ্বনি (বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় বর্ণ ইত্যাদি)কখনাে কখনাে সঘােষ ধ্বনি (বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ ইত্যাদি)হয়ে
যায়। যেমন—ছত্র > ছাত > ছাদ।
(ছ) ‘ল’ কোথাও কোথাও 'ন' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন-লবণ > নুন, লুচি > নুচি, লৌহ > নােয়া।
(২)রাঢ়ী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :
(ক) কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকে বহুবচনে -'দের' বিভক্তি যােগ হয়।
যেমন : কর্মকারক--আমাদের বই দাও। করণকারক--তােমাদের দ্বারা একাজ হবে না।
(খ) সাধারণত সকর্মক ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে—মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম। রাঢ়ীতে গৌণ
কর্মের বিভক্তি হচ্ছে ‘কে’ এবং মুখ্য কর্মে কোনাে বিভক্তি যােগ হয় না।
যেমন—আমি রামকে (গৌণকর্ম) টাকা (মুখ্য কর্ম) ধার দিয়েছি।
(গ) অধিকরণ কারকে ‘এ’ এবং ‘-তে বিভক্তির প্রয়ােগ হয়।
যেমন- ঘরেতে ভ্রমর এলাে গুণগুণিয়ে।
গজদন্ত-মিনারে বসে জনতার প্রতি প্রেমের বাণী
প্রচার করা ঠিক নয়, বিবেকানন্দের মতাে সারা দেশ পায়ে হেঁটে দেখতে হবে।
(ঘ) সদ্য অতীত কালে প্রথম পুরুষের অকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি হল 'ল'।
যেমন—সে গেল = He went) ;
কিন্তু সকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি হল ‘-লে’
(যেমন—সে বললে = He said)।
সদ্য অতীত কালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার
বিভক্তি হল ‘লুম’
(যেমন—আমি বললুম = I said)
(ঙ) মূল ধাতুর সঙ্গে ‘আছ’ ধাতু যােগ করে সেই আছ ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষের বিভক্তি যােগ করে ঘটমান বর্তমান ও ঘটমান অতীতের রূপ গঠন করা হয়।
যেমন- কর + ছি = করছি (আমি করছি),
কর + ছিল = করছিল। (সে করছিল)।
Q:- বরেন্দ্রী উপভাষার অঞ্চল বা এলাকা উল্লেখ করে এই উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ।
বরেন্দ্রী উপভাষার ভৌগলিক অঞ্চল :
জলপাইগুড়ি, মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহী পাবনা।
বরেন্দ্রী উপভাষার pdf download here
ভাষা হল মানুষের যোগাযোগের সহজাত মাধ্যম বা বাহনই হল ভাষা। ভাষার সংজ্ঞায়ন করতে হলে, যে সংজ্ঞাটি সবার প্রথমে মাথায় আসে; তা হল, মানুষের বাকযন্ত্র থেকে উৎপন্ন এবং ভাবপ্রকাশে সক্ষম অর্থবোধক ধ্বনিকে বলা হয় ভাষা।
তবে ভাষা শুধুমাত্র মৌখিক কোন বিষয় নয়, বরং লিখিত শব্দ (letters), অঙ্গভঙ্গিও ভাষা হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ, ভাষা হল অঙ্গভঙ্গি, মৌখিক শব্দ বা লিখিত শব্দের মাধ্যমে যোগাযোগের একটি প্রতীকী মাধ্যম, যা কিনা অর্থ প্রকাশে সক্ষম।
1)ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, মনুষ্য জাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনি সকল দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, তাকে ভাষা বলে।
2)ড. সুকুমার সেনের মতে, মনের ভাব প্রকাশ করার নিমিত্ত বিভিন্ন জাতির বা সমাজের সকল সভ্যের বোধগম্য বাক্যসমূহের সমষ্টিকে ভাষা
3)ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোন বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্তি শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে।
4)ড. মুহম্মদ আবদুল হাই এর মতে, এক এক সমাজের সকল মানুষের অর্থবোধক ধ্বনির সমষ্টিই ভাষা।
সুতরাং বলা যায়, বাগযন্ত্রের সাহায্যে (নাক, কন্ঠ, তালু,দাঁত, জিহ্বা ইত্যাদি) উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনি সমষ্টিই হলো ভাষা।
ভাষার বৈশিষ্ট্য:
1.যে কোন ধ্বনি বা শব্দ মাত্রই ভাষা নয়; বরং, শুধুমাত্র বোধগম্য ধ্বনি বা শব্দই হল ভাষার মূল।
2.ভাষা অবশ্যই অর্থপূর্ণ হবে।
3.পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম।
4.ভাষা বক্তব্যের অন্তর্গত রূপকে প্রকাশ করে।
5.ভাষা মানুষের স্বভাব, সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে প্রকাশ করে।
6.একটি বিশেষ সম্প্রদায়, জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ও ব্যবহৃত ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে একটি ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
7.মানুষের স্বেচ্ছাকৃত আচরণ ও অভ্যাসের সমষ্টি হল ভাষা।
8.ভাষা হল মানুষের স্বেচ্ছাকৃত আচরণ ও অভ্যাসের সমষ্টি।
9.ধ্বনি, শব্দ, পদ ও বাক্যের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ গাঠনিক পর্যায়কে রক্ষাকারী শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল ভাষা।
10.দেশ, কাল ও পরিবেশভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে থাকে।
ভাষার মূল অংশ:
পৃথিবীর যেকোন ভাষাকে বিশ্লেষণ করা হলে মৌলিক উপাদান হিসেবে মূলত ৪ টি অংশ পাওয়া যায়। এরা হল-
• ধ্বনি (sound)
• শব্দ (word)
• বাক্য (sentence)
• অর্থ (meaning)
ধ্বনি হল ভাষার সবচেয়ে মৌলিক বা মূল উপাদান। ধ্বনি, মূলত ভাষার মৌখিকরূপ প্রকাশক উপাদান, আর এই মৌখিক উপাদানের লিখিত চিহ্নই বা symbol হল বর্ণ।
একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় শব্দ। তবে একাধিক শব্দকে ব্যকরনের নিয়ম মাফিক গঠন করা হলে তা থেকে উৎপন্ন হয় বাক্য এবং যা মূলত ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষা তৈরি করে, যা আমাদের কাছে মূলত অর্থ প্রকাশ করে থাকে।
[ ] বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়,
ভাষার মৌলিক উপাদান বা ক্ষুদ্রতম একক হল ধ্বনি বা বর্ণ; ভাষার মূল উপকরণ, একক বা বৃহত্তম একক হল বাক্য।
পৃথিবীতে বর্তমানে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা নির্ভূল্ভাবে ঠিক কতটি তার সঠিক কোন হিসাব নেই; তবে ভাষা বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী পৃথিবীতে বর্তমানে সাড়ে ৩ হাজারেরও বেশি ভাষা প্রচলিত আছে।
উপভাষা কাকে বলে? কয় প্রকার ও কি কি?? তাদের সীমানা নির্ধারণ কর।
ভাষা কাকে বলে? ভাষার বৈশিষ্ট্য ও অংশ
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 1st semester 1 ও 2 paper suggetion
পারিভাষিক শব্দ কি বা কাকে বলে | পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজনীয়তা ও পরিভাষা তালিকা
ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি | dhoni poribortoner riti mcq|primary TET
ভারতীয় ভাষা পরিষদ l Bhartiya -arya Bhasha
জীবনস্মৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । rabindra nath tagor jibon sriti
বরেন্দ্রী উপভাষার অঞ্চল বা এলাকা উল্লেখ করে এই উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ।